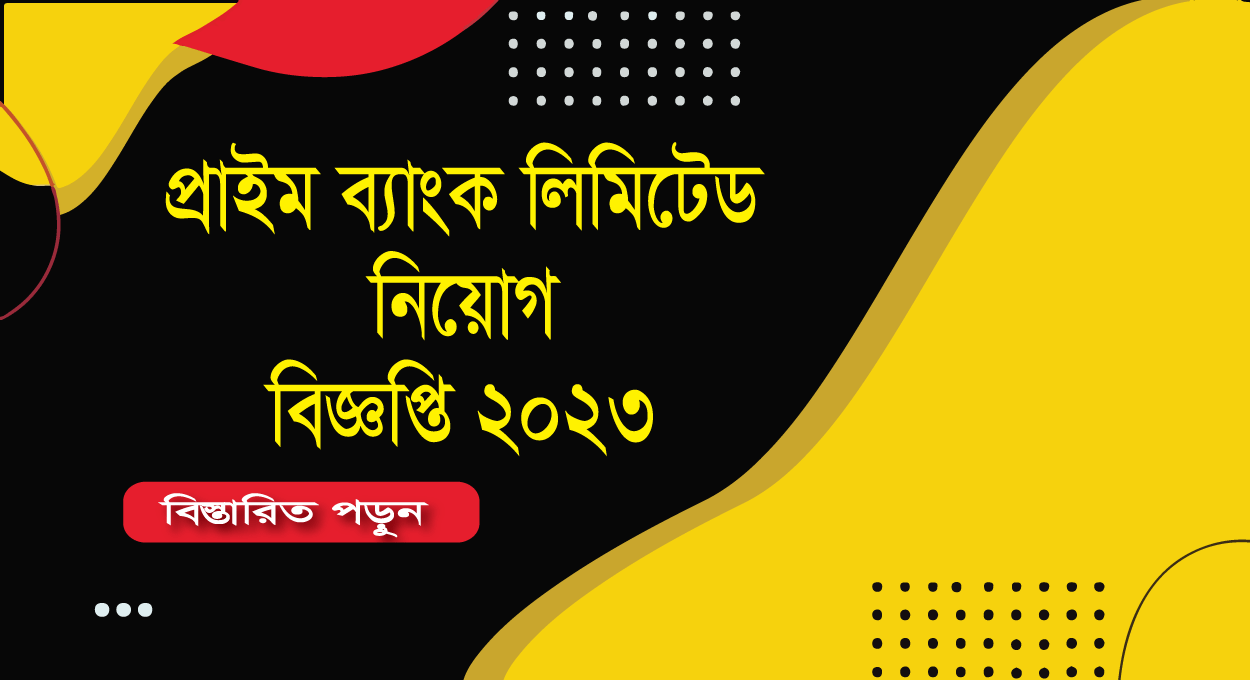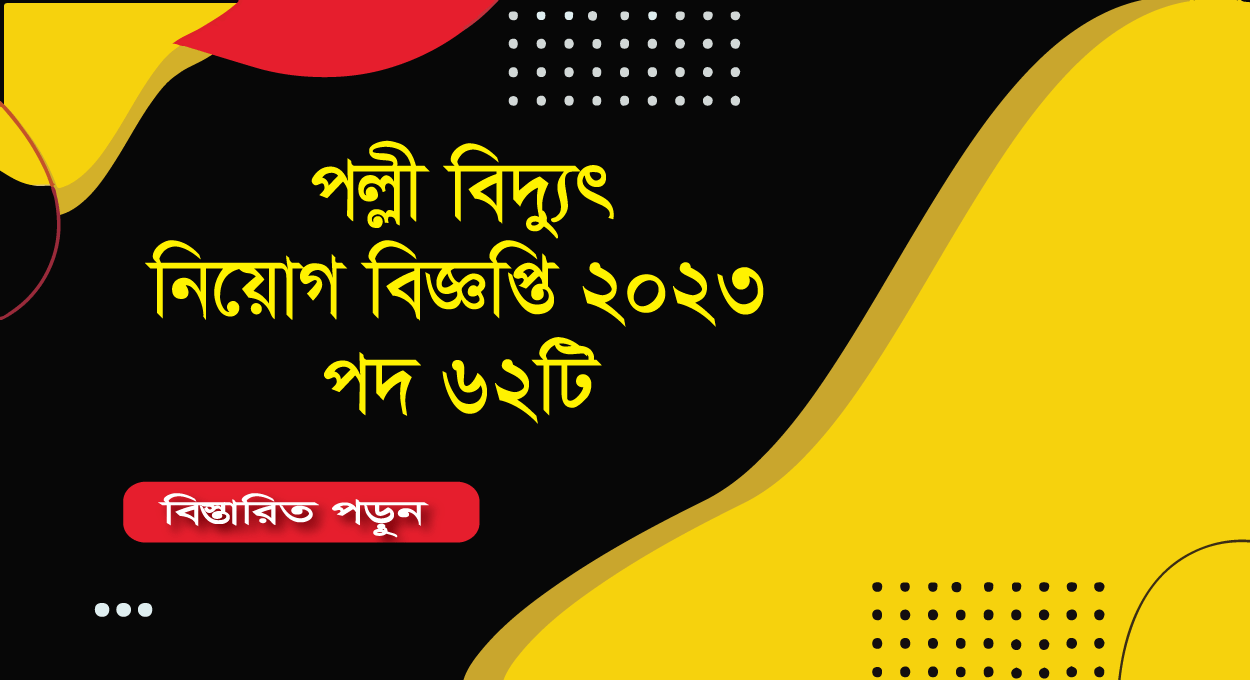ধ্বনি-পরিবর্তন
কথা বলার সময় অনেক শব্দের উচ্চারণ পাল্টে যায়। যেমন রিকশা’ শব্দটি কারও কারও উচ্চারণে ‘রিশকা’ হয়ে যেতে পারে। ধ্বনি-পরিবর্তনে সাধারণভাবে অর্থের পরিবর্তন ঘটে না। যেমন ‘গ্রাম’ বা ‘গেরাম’ শব্দ দুটি একই অর্থ বহন করে। তবে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত শব্দটি ভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা তৈরি করে। যেমন ‘প্রীতি ও ‘পিরিতি’ শব্দ দুটি অনুরূপ সমান অর্থে প্রয়ােগ করা হয়। না। ধ্বনি-পরিবর্তন সব মৌখিক ভাষার ক্ষেত্রেই একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।ধ্বনি-পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ রয়েছে :
- সময়ের প্রবাহ
- আঞ্চলিক পার্থক্য
- বাগযন্ত্রের ক্রটি
- অন্য ভাষার প্রভাব
- দ্রুত উচ্চারণ
- উচ্চারণে অসাবধানতা ইত্যাদি।
বিসিএস প্রস্তুতি: স্বরধ্বনির পরিবর্তন
১. স্বরাগম
স্বরাগম মানে স্বরের আগমন। শব্দে স্বরধ্বনির আগমনকে স্বরাগম বলে। স্বরাগম তিন ধরনের।ক. আদি স্বরাগম :
এ ক্ষেত্রে শব্দের শুরুতে স্বরের আগমন ঘটে। যেমন স্কুল > ইস্কুল; স্তাবল > আস্তাবল।। এখানে প্রথম শব্দের শুরুতে ই এবং দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে আ ধ্বনির আগমন ঘটেছে শব্দের শুরুতে। যুক্তাক্ষর থাকলে উচ্চারণ কঠিন হয়। তখন আদি স্বরাগম ঘটতে দেখা যায়।।খ. মধ্য স্বরাগম :
মধ্য স্বরাগমের আরেক নাম বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। মধ্য স্বরাগমে শব্দের মাঝখানে স্বর আসে। যেমন, রত্ন > রতন; স্বপ্ন > স্বপন। এখানে প্রথম শব্দে ত ত-এর সঙ্গে একটি অ ধ্বনি যুক্ত হয়েছে; একইভাবে। দ্বিতীয় শব্দে প-এর সঙ্গে একটি অ ধ্বনি যুক্ত হয়েছে। ৬ তিন ধরনের স্বরাগমের মধ্যে মধ্য স্বরাগম বেশি ঘটে থাকে।গ. অন্ত্য স্বরাগম :
শব্দের শেষে স্বরের আগমনকে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন দিশ > দিশা; বেঞ্চ > বেঞ্চি। প্রথম উদাহরণে শব্দের শেষে আ ধ্বনি এবং দ্বিতীয় উদাহরণে শব্দের শেষে ই ধ্বনির আগমন ঘটেছে। শব্দ এক সিলেবলের হলে উচ্চারণ করা কষ্টকর হয়। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত শব্দের শেষে স্বরের আগমন ঘটে থাকে।২. স্বরলােপ
স্বরধ্বনির লােপকে বলা হয় স্বরলােপ। স্বরলােপের আরেক নাম সমপ্রকর্ষ। স্বরলােপ হলাে স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া। স্বরলােপও তিন ধরনের।ক. আদি স্বরলােপ :
এ ক্ষেত্রে শব্দের প্রথম স্বরটি লােপ পায়। যেমন অলাবু > লাবু > লাউ। এখানে সংস্কৃত ‘অলাবু’ শব্দের অ লােপ পেয়ে ‘লাবু হয়েছে। লাবু থেকে পরবর্তী ধাপে আবার ব্যঞ্জনের লােপ ঘটে ‘লাউ’ হয়েছে।খ. মধ্য স্বরলােপ :
মধ্য স্বরলােপে শব্দের মাঝখানের স্বরটি লােপ পায়। যেমন সুবর্ণ > সবর্ণ > স্বর্ণ। এখানে শব্দের ভেতরের ‘উ’ ধ্বনি লােপ পেয়ে সবর্ণ হয়েছে। পরে সবর্ণ থেকে স্বর্ণ হয়েছে।গ. অন্ত্য স্বরলােপ :
এ ক্ষেত্রে শব্দের শেষের স্বরটি লােপ পায়। যেমন আশা > আশ; আজি > আজ। প্রথম উদাহরণে আ এবং দ্বিতীয় উদাহরণে ই লােপ পেয়েছে।৩. অসমীকরণ
একই শব্দের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় অসমীকরণ। যেমন ধপ + ধপ > ধপাধপ; টপ + টপ > টপাটপ। অসমীকরণে শব্দের ভেতর সাধারণত আ ধ্বনি যুক্ত হতে দেখা যায়। অসমীকরণ একধরনের মধ্য স্বরাগম। তবে মধ্য স্বরাগমের সঙ্গে পার্থক্য হলাে, এখানে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকে।৪. অপিনিহিতি
পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্তব্যঞ্জনের আগে ‘ই’ বা ‘উ’ উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন আজি > আইজ; বাক্য > বাইক্য। প্রথম উদাহরণে শব্দের শেষের ই ধ্বনি আগেই উচ্চারিত হয়েছে; দ্বিতীয় উদাহরণে যুক্তধ্বনির আগে ই উচ্চারিত হয়েছে। অপিনিহিতি মূলত ই এবং উ ধ্বনির ব্যাপার। বাংলা শব্দে প্রচুর পরিমাণে অপিনিহিতি ঘটতে দেখা যায়।৫. অভিশ্রুতি
বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে গেলে এবং সে অনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে। তাকে বলে অভিশ্রুতি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর নাম দিয়েছেন অভ্যন্তর সন্ধি। যেমন বলিয়া বইল্যা > বলে। এই উদাহরণের প্রথম ধাপে ঘটেছে অপিনিহিতি; এরপর হয়েছে অভিশ্রুতি। বাংলা ক্রিয়াপদ সাধু থেকে। চলিত হওয়ার সময় দুই ধাপে ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটে।। প্রথম ধাপে হয়. অপিনিহিতি এবং পরের ধাপে হয়। অভিশ্রুতি। অভিশ্রুতিকে অভ্যন্তর সন্ধিও বলে। কারণ, বইল্যা > বলে উদাহরণে ল-এর আগের ই এবং ল-এর পরের অ্যা মিলে ‘এ’ ধ্বনি তৈরি হয়েছে।৬. স্বরসংগতি
একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে পাশের স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসংগতি বলে। স্বরসংগতি কেন হয়, সেটা বােঝার জন্য উচ্চ স্বরধ্বনি এবং নিম্ন স্বরধ্বনি। সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। ই এবং উ উচ্চ স্বরধ্বনি; এ, অ্যা, অ, ও— এগুলাে মধ্য স্বরধ্বনি এবং আ নিম্ন স্বরধ্বনি। স্বরসংগতি তিন ধরনের।ক. প্রগত স্বরসংগতি :
এ ক্ষেত্রে আগের ধ্বনির প্রভাবে পরের ধ্বনির পরিবর্তন হয়। যেমন মুলা > মুলাে; শিকা > শিকে। প্রথম উদাহরণে উচ্চ স্বরধ্বনি উ-এর প্রভাবে নিম্ন স্বরধ্বনি আ বদলে ও হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে উচ্চ স্বরধ্বনি ই-এর প্রভাবে নিম্ন স্বরধ্বনি আ বদলে এ হয়েছে।খ. পরাগত স্বরসংগতি:
পরাগত স্বরসংগতিতে পরের ধ্বনির প্রভাবে আগের ধ্বনির পরিবর্তন হয়। যেমন দেশি > দিশি; মিঠাই > মেঠাই। প্রথম উদাহরণে উচ্চ স্বরধ্বনি ই-এর প্রভাবে এ বদলে ই হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে নিম্ন স্বরধ্বনি আ-এর প্রভাবে ই বদলে এ হয়েছে।গ. মধ্যগত স্বরসংগতি:
পাশের দুই ধ্বনির প্রভাবে মাঝখানের ধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়। যেমন বিলাতি > বিলিতি। এখানে দুই পাশের দুটি উচ্চ স্বরধ্বনির প্রভাবে মাঝখানের নিম্ন স্বরধ্বনি আ বদলে ই হয়েছে।ঘ. অন্যোন্য বা পারস্পরিক স্বরসংগতি :
এ ক্ষেত্রে দুটি ধ্বনিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। যেমন মােজা > মুজো। এখানে ও ধ্বনি বদলে উ হয়েছে এবং আ ধ্বনি। বদলে ও হয়েছে।বিসিএস প্রস্তুতি: ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন
১. সমীভবন
দুটি ভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি একে অপরের প্রভাবে কমবেশি পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনকে বলা হয় সমীভবন। সমীভবন তিন ধরনের।ক. প্রগত সমীভবন :
আগের ধ্বনির প্রভাবে পরের ধ্বনির পরিবর্তন হয়। যেমন চক্র > চক। এখানে আগের ক ধ্বনির প্রভাবে পরের র বদলে ক হয়েছে।খ. পরাগত সমীভবন :
পরের ধ্বনির প্রভাবে আগের ধ্বনির পরিবর্তন হয়। যেমন বিপদ + জনক > বিপজ্জনক। এখানে পরের জ ধ্বনির প্রভাবে আর দ বদলে জ হয়েছে।গ. অনন্যান্য বা পারস্পরিক সমীভবন:
দুটি ধ্বনিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। যেমন সত্য > সচ্চ। এখানে ত এবং য ধ্বনি বদলে চ্চ হয়েছে।বিসিএস বাংলা প্রস্তুতি
২. বিষমীভবন
বিষমীভবনে দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন হয়; অন্যটির পরিবর্তন হয় না। যেমন শরীর > শরীল। এখানে প্রথম র-এর পরিবর্তন হয়নি; দ্বিতীয় র-এর পরিবর্তন হয়েছে। সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়ার নাম বিষমীভবন।৩. ধ্বনি-বিপর্যয়
শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পরের স্থানবদল ঘটলে তাকে ধ্বনি-বিপর্যয় বলে। যেমন রিকশা > রিশকা; বাকস > বাসক। প্রথম উদাহরণে ক এবং শ ধ্বনির পারস্পরিক স্থানবদল ঘটেছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ক এবং স ধ্বনির পারস্পরিক স্থানবদল ঘটেছে। Tipscenter24.com৪. ব্যঞ্জনদ্বিত্ব
একটি ব্যঞ্জন দুবার উচ্চারিত হলে তাকে বলে দ্বিত্বব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব। যেমন সকাল > সকাল; ছােট > ছােট্ট। প্রথম উদাহরণে ক ধ্বনি এবং দ্বিতীয় উদাহরণে ট ধ্বনি দুবার উচ্চারিত হয়েছে।৫. ব্যঞ্জনচ্যুতি
এ ক্ষেত্রে দুটি একই রকম ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি লােপ পায়। যেমন বড়দাদা > বড়দা; ছােটদিদি > ছােড়দি। প্রথম উদাহরণে দুটি দা-এর একটি লােপ পেয়েছে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে দুটি দি-এর একটি লােপ পেয়েছে।৬. অন্তর্হতি
শব্দের মধ্যে কোনাে ব্যঞ্জনধ্বনি লােপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন ফাল্গুন > ফাগুন; ফলাহার > ফলার। প্রথম উদাহরণে ল এবং দ্বিতীয় উদাহরণে হা লােপ পেয়েছে।৭. ব্যঞ্জনবিকৃতি
আঞ্চলিক উচ্চারণে অনেক সময় দেখা যায়, একটি ব্যঞ্জনধ্বনির বদলে কাছাকাছি আরেকটি ব্যঞ্জনধ্বনি চলে আসে। একে বলে ব্যঞ্জনবিকৃতি। যেমন ধাইমা > দাইমা; আপেল > আফেল। প্রথম উদাহরণে ধ বদলে দ হয়েছে; দ্বিতীয় উদাহরণে প বদলে ফ হয়েছে।FAQ: বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি বাংলা সর্ম্পকিত আপনার প্রশ্ন ও উত্তর:
স্বরাগম কাকে বলে?
স্বরাগম মানে স্বরের আগমন। শব্দে স্বরধ্বনির আগমনকে স্বরাগম বলে। স্বরাগম তিন ধরনের।
অন্ত্য স্বরাগম কাকে বলে?
শব্দের শেষে স্বরের আগমনকে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন দিশ > দিশা; বেঞ্চ > বেঞ্চি। প্রথম উদাহরণে শব্দের শেষে আ ধ্বনি এবং দ্বিতীয় উদাহরণে শব্দের শেষে ই ধ্বনির আগমন ঘটেছে। শব্দ এক সিলেবলের হলে উচ্চারণ করা কষ্টকর হয়। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত শব্দের শেষে স্বরের আগমন ঘটে থাকে।
স্বরলােপ কাকে বলে?
স্বরধ্বনির লােপকে বলা হয় স্বরলােপ। স্বরলােপের আরেক নাম সমপ্রকর্ষ। স্বরলােপ হলাে স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া।
ধ্বনি-বিপর্যয় কাকে বলে?
শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পরের স্থানবদল ঘটলে তাকে ধ্বনি-বিপর্যয় বলে।
দ্বিত্বব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব কাকে বলে?
একটি ব্যঞ্জন দুবার উচ্চারিত হলে তাকে বলে দ্বিত্বব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব।